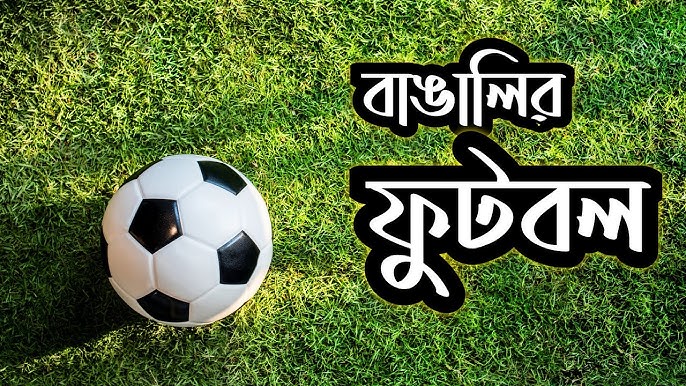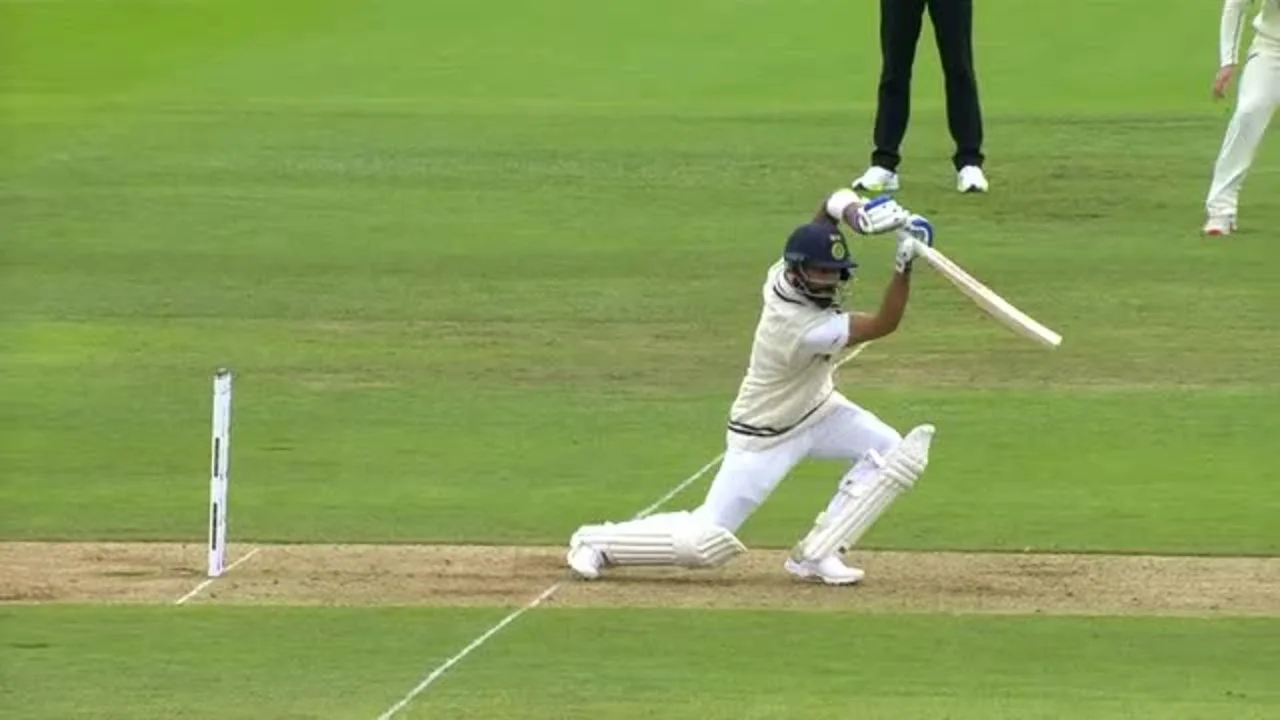ফুটবল! এই একটি শব্দই যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আবেগ, উত্তেজনা, আনন্দ এবং বিষাদকে এক সুতোয় গেঁথে ফেলার ক্ষমতা রাখে। ৯০ মিনিটের এই খেলার জাদুতে মোহিত হয় গোটা বিশ্ব, কিন্তু কিছু কিছু ভূখণ্ডে এই খেলাটা নিছক বিনোদন নয়, বরং সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর সেই মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ বা বাঙালির অবস্থান একেবারে শীর্ষে। এখানে ফুটবল শুধু চামড়ার গোলককে পায়ে ঘোরানোর কৌশল নয়, এটি বাঙালির শিরায়-ধমনীতে প্রবাহিত এক জীবন্ত আবেগ। এটি এমন এক ভাষা, যা দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালি তার সুখ-দুঃখ, লড়াই এবং ঐক্যের গল্প বলে এসেছে।
বাঙালির ফুটবল প্রেমকে বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের পাতায়। একটা সময় ছিল, যখন ভারতীয় ফুটবল বিশ্বমঞ্চে সমীহ আদায় করত। পঞ্চাশ ও ষাটের দশককে ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগ বলা হয় এবং সেই যুগের শিরদাঁড়া ছিলেন বাঙালি ফুটবলাররা। শৈলেন মান্নার অধিনায়কত্বে ভারত ১৯৫১ সালের এশিয়ান গেমসে সোনা জেতে। ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতের চতুর্থ স্থান অধিকার করাটা আজও এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। সেই দলের প্রাণভোমরা ছিলেন চুনী গোস্বামী, পি.কে. ব্যানার্জী, Neville D’Souza-র মতো কিংবদন্তীরা। খালি পায়ে ব্রিটিশদের হারিয়ে মোহনবাগানের আই.এফ.এ. শিল্ড জয় কেবল একটি ক্লাবের জয় ছিল না, ছিল পরাধীন এক জাতির ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার প্রতীক। সেই জয় বাঙালির আত্মসম্মান এবং জাতীয়তাবাদী চেতনাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটই বাঙালির ফুটবল আবেগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল, যা আজও অটুট।
তবে বাঙালির ফুটবল আবেগের সবচেয়ে জীবন্ত এবং বর্ণময় অধ্যায়টি লেখা হয় ময়দানের সবুজ ঘাসে, যেখানে দুটি রঙ এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় আবার একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াইয়ে মত্ত হয় – সবুজ-মেরুন এবং লাল-হলুদ। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। এই দুটি ক্লাব শুধু দুটি ফুটবল দল নয়, এ হলো বাঙালির সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিভাজনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। একদিকে মোহনবাগান, যারা এদেশের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা ‘ঘটি’দের আবেগের প্রতীক। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল, দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আসা ‘বাঙাল’দের লড়াই, অস্তিত্ব এবং ঐতিহ্যের ধারক। তাই যখন এই দুই দল মাঠে নামে, তখন সেটা আর নিছক একটা ফুটবল ম্যাচ থাকে না, হয়ে ওঠে আত্মসম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এক মহাযুদ্ধ।
কলকাতা ডার্বির দিন গোটা শহর যেন এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। রাস্তাঘাট, অলিগলি, চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বাড়ির ছাদ পর্যন্ত এই দুই রঙে ছেয়ে যায়। ম্যাচের কয়েক দিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় কথার লড়াই, চলতে থাকে ইতিহাস আর পরিসংখ্যানের চুলচেরা বিশ্লেষণ। ম্যাচের দিন সমর্থকদের মিছিল করে স্টেডিয়ামের দিকে এগিয়ে যাওয়া, মুখে স্লোগান, হাতে পতাকা – এই দৃশ্য এককথায় অনবদ্য। গ্যালারিতে বসে সমর্থকদের সেই আকাশ কাঁপানো চিৎকার, প্রিয় দলের প্রতিটি গোলের পর বাঁধভাঙা উল্লাস কিংবা হারের পর শ্মশানের নিস্তব্ধতা – এই সবই ডার্বির মহাকাব্যের অংশ। এই আবেগের আঁচ এতটাই তীব্র যে তা রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মোহনবাগান জিতলে ঘটিদের বাড়িতে উদযাপিত হয় চিংড়ির উৎসব, আর ইস্টবেঙ্গল জিতলে বাঙালদের ঘরে রান্না হয় ইলিশ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কয়েক দশক ধরে বাঙালিকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, একে অপরের সাথে তর্ক করতে শিখিয়েছে, কিন্তু দিনের শেষে এই ফুটবলই তাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।
এই প্রাতিষ্ঠানিক ফুটবলের সমান্তরালে বয়ে চলে আরেকটা জগৎ – আমাদের পাড়ার ফুটবল। বর্ষার বিকেলে কাদা মাখা মাঠে, ইঁটের গোলপোস্ট বানিয়ে যে খেলার শুরু, সেখানেই ফুটবলের প্রতি আসল ভালোবাসা জন্মায়। এখানে কোনো রেফারি নেই, অফসাইডের নিয়ম বড় গোলমেলে, কিন্তু আবেগ আর জেতার খিদে কোনো অংশে কম নয়। এই পাড়ার মাঠগুলোই প্রতিভার আঁতুড়ঘর। এখান থেকেই উঠে আসে অসংখ্য প্রতিভা। এই সংস্কৃতিরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ‘খেপ খেলা’। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে টুর্নামেন্টে টাকার বিনিময়ে খেলতে যাওয়া এই ‘খেপ’ খেলোয়াড়রা স্থানীয় কিংবদন্তীতে পরিণত হন। হয়তো জাতীয় স্তরে তারা পরিচিতি পান না, কিন্তু নিজেদের অঞ্চলে তাদের জনপ্রিয়তা কোনো অংশে কম নয়। এই তৃণমূল স্তরের ফুটবলই বাংলার ফুটবল সংস্কৃতির আসল প্রাণশক্তি।
তবে বাঙালির ফুটবল আবেগ শুধু ময়দান বা পাড়ার মাঠেই সীমাবদ্ধ নেই। যখন বিশ্বকাপের সময় আসে, তখন গোটা বাংলা যেন এক বিশ্বগ্রাম হয়ে ওঠে। এখানে চিরন্তন লড়াইটা চলে মূলত দুটি দেশের মধ্যে – ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা। হলুদ-সবুজ এবং আকাশি-সাদার পতাকায় ছেয়ে যায় গোটা রাজ্য। দিয়েগো মারাদোনা এবং পেলে এখানকার মানুষের কাছে ফুটবলার নন, তাঁরা হলেন পূজনীয় দেবতা। পরবর্তীকালে সেই জায়গা নিয়েছেন লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বা নেইমারের মতো তারকারা। বিশ্বকাপের সময় মধ্যরাতে পাড়ার মোড়ে মোড়ে জায়ান্ট স্ক্রিনে খেলা দেখা, গোল হলে পটকা ফাটানো, প্রিয় দল জিতলে বিজয় মিছিল বের করা – এই সবই বাঙালির ফুটবল উৎসবের অংশ। চায়ের দোকানে তর্কের ঝড় ওঠে – কার শিল্প migliore, মেসির ড্রিবলিং নাকি রোনাল্ডোর গোল করার ক্ষমতা? এই তর্ক কখনও শেষ হয় না, কারণ এটা যুক্তির চেয়েও বেশি আবেগের। ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের প্রসারও বাঙালির ফুটবলচর্চায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল, রিয়াল মাদ্রিদ বা বার্সেলোনার ম্যাচ নিয়েও একই রকম উন্মাদনা দেখা যায়।
তবে এই আবেগের আড়ালে একটা দীর্ঘশ্বাসও লুকিয়ে আছে। স্বর্ণযুগের পর ভারতীয় ফুটবলের মানচিত্রে বাংলার দাপট অনেকটাই কমেছে। জাতীয় দলে বাঙালি খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমেছে, পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং সঠিক পরিকল্পনার অভাবে অনেক প্রতিভা মাঝপথেই হারিয়ে যায়। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (ISL) ভারতীয় ফুটবলে নতুন পেশাদারিত্ব এবং চাকচিক্য নিয়ে এলেও, তা বাংলার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব সংস্কৃতিকে কতটা সাহায্য করেছে, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের আইএসএলে অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, যা সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে আশা জাগিয়েছে। সুনীল ছেত্রীর মতো কিংবদন্তীর বিদায়ের পর ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ কাদের হাতে, সেই প্রশ্নও উঠছে। তবে আশা এটাই যে, নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়রা বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য নিজেদের উজাড় করে দেবে।
পরিশেষে বলা যায়, সময় বদলেছে, খেলার ধরণ বদলেছে, নতুন নতুন তারকা এসেছেন, কিন্তু বাঙালির জীবনে ফুটবলের স্থান বদলায়নি। ফুটবল বাঙালির কাছে শুধু ৯০ মিনিটের খেলা নয়, এটি একটি সংস্কৃতি, একটি ঐতিহ্য এবং এক জীবনদর্শন। এটি আমাদের শেখায় কীভাবে হারকে মেনে নিয়ে আবার নতুন করে লড়াই শুরু করতে হয়, কীভাবে দলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হয় এবং কীভাবে হাজারো বিভেদের মাঝেও একটা共同 আবেগের ছাতার তলায় একত্রিত হতে হয়। যতদিন ময়দানে বল গড়াবে, যতদিন গ্যালারিতে সমর্থকদের গর্জন শোনা যাবে, ততদিন বাঙালির রক্তে ফুটবল তার নিজস্ব ছন্দে স্পন্দিত হতে থাকবে। এই আবেগ অমর, এই ভালোবাসা চিরন্তন।